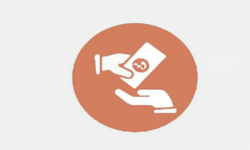প্রতিবেদক: সঞ্চয়পত্রের সুদহার কমানোর সিদ্ধান্ত গত সোমবার কার্যকর হওয়ার পর সাধারণ সঞ্চয়কারীদের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। দেশের অবসরপ্রাপ্ত ও বয়স্ক জনগোষ্ঠীর বড় অংশের মাসিক খরচের মূল উৎস এই সঞ্চয়পত্রের সুদ। ফলে সুদহার কমে যাওয়া তাঁদের জন্য এক ধরনের অর্থনৈতিক অশনিসংকেত।
আয় কমলে মানুষের প্রথম পদক্ষেপ হয় খরচ কমানো। গবেষণায় দেখা গেছে, এ ধরনের পরিস্থিতিতে ভোগব্যয় বিশেষ করে খাবারের মান ও পরিমাণ কমে যায়। উচ্চ মূল্যস্ফীতির সময়ে এই আয় হ্রাস আরও ভয়াবহ প্রভাব ফেলতে পারে। সাংবাদিক আফসান চৌধুরীর একটি ফেসবুক পোস্টে এই বাস্তবতার প্রতিফলন পাওয়া যায়। তিনি লেখেন, “সঞ্চয়পত্রের সুদের হার কমালো। আমার মতো মানুষের জন্য বড় ধাক্কা। আমার তো পেনশন বা পৈতৃক সোনার ব্যবসা নাই।” পরে তিনি মন্তব্য করেন, “মনটা খারাপ। আয়ের সবচেয়ে বড় উৎস সংকুচিত হলো। মন্ত্রীরা সবাই সচ্ছল, তারা কীভাবে এই কষ্ট বুঝবে?”
বাংলাদেশে পার্সোনাল ফাইন্যান্স বিষয়টি এখনো পর্যাপ্ত গুরুত্ব পায়নি। সরকারি চাকরিজীবী ছাড়া অন্য কেউ সাধারণত পেনশনের আওতায় ছিলেন না। ২০২৩ সালে সর্বজনীন পেনশন চালু হলেও তা এখনো জনপ্রিয় হয়নি। বিমা কোম্পানির পেনশন প্রকল্প থাকলেও অধিকাংশ মানুষ তার সম্পর্কে জানেন না কিংবা আস্থাহীনতায় এগিয়ে যান না।
মূলত বেসরকারি খাত ও সরকারি খাতের নিচের স্তরের কর্মজীবীদের আয় মূল্যস্ফীতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণভাবে বাড়েনি। দুই বছরের বেশি সময় ধরে চলা উচ্চ মূল্যস্ফীতির প্রভাবে সঞ্চয়ের সামর্থ্য কমে গেছে। সংসার চালাতে হিমশিম খেতে হয়, সঞ্চয় তো বিলাসিতা। জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরের তথ্যে দেখা যায়, এপ্রিল মাসে সঞ্চয়পত্র বিক্রি মার্চের তুলনায় প্রায় ৭ শতাংশ কমেছে, যদিও সঞ্চয়পত্র ভাঙানোর হার কমেছে ২৬ শতাংশ। তবু চলতি অর্থবছরের প্রথম ১০ মাসে সাড়ে সাত হাজার কোটি টাকার নিট বিক্রি ঋণাত্মক, অর্থাৎ ভাঙানোর পরিমাণ বিনিয়োগের চেয়ে বেশি।
এই পরিসংখ্যান স্পষ্ট করে যে, দেশের মানুষ আয়ের চেয়ে বেশি ব্যয়ে বাধ্য হচ্ছে, ফলে সঞ্চয় কমে যাচ্ছে। বেসরকারি চাকরিজীবী ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা বয়সের শেষ ভাগে দুর্বিষহ জীবনে পড়েন। সরকার পেনশন চালু করলেও এর প্রচার ও গ্রহণযোগ্যতা বাড়ানো দরকার। বিমা কোম্পানিগুলোর পেনশন প্রকল্পেও আস্থা ও সচেতনতা আনতে সম্মিলিত উদ্যোগ প্রয়োজন।
বাংলাদেশে সঞ্চয়প্রবণতা কম, মানুষের মধ্যে অদৃষ্টবাদী মানসিকতা আছে। যেমন—“মুখ দেবেন যিনি, আহারও দেবেন তিনি”—এই মানসিকতার প্রভাব এখনো রয়েছে। এর সঙ্গে যোগ হয়েছে জিডিপি প্রবৃদ্ধির সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ মূল্যস্ফীতি। নিম্ন ও মধ্যবিত্ত মানুষের জীবনে তাই ক্রমাগত অনিশ্চয়তা বাড়ছে।
অন্যদিকে, বিমা খাতের দীর্ঘমেয়াদি তহবিল অবকাঠামো উন্নয়ন ও পুঁজিবাজারে বিনিয়োগে ব্যবহার করা যায়। অথচ দেশে বিমা খাতও কাঙ্ক্ষিত বিকাশ পায়নি।
যদিও গত এক দশকে জিডিপির প্রবৃদ্ধি ছিল ৬ শতাংশের বেশি, তবে জীবনযাত্রার মান নিয়ে প্রশ্ন থেকেই গেছে। বিশ্ব ব্যাংকের পূর্বাভাস অনুযায়ী, চলতি বছর চরম দারিদ্র্য ৩০ লাখ মানুষ পর্যন্ত বেড়ে যেতে পারে। এর মধ্যেই সঞ্চয়পত্রের সুদহার কমানো মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা হয়ে এসেছে।
উচ্চ মূল্যস্ফীতির সময় সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হন নিম্ন ও সীমিত আয়ের মানুষ। তাই অনেক দেশ এ শ্রেণিকে রক্ষা করতে বিভিন্ন কর্মসূচি হাতে নেয়। উদাহরণস্বরূপ—শ্রীলঙ্কার ‘অম্মসুমা’ নগদ সহায়তা কর্মসূচি এবং পাকিস্তানের ‘এহসাস কর্মসূচি’, যা ১.৫ কোটি পরিবারকে নগদ সহায়তা দিয়ে দারিদ্র্য বিমোচনে ভূমিকা রেখেছে। ভারতে ‘আধার কার্ড’ ব্যবহার করে সরকার প্রয়োজন অনুযায়ী নগদ সহায়তা দিতে পারে।
বাংলাদেশে কিছু সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি থাকলেও তা খুবই সীমিত। টিসিবি কার্ড ও ট্রাক সেলের মতো উদ্যোগ ছাড়া উচ্চ মূল্যস্ফীতির মোকাবিলায় তেমন কার্যকর কর্মসূচি নেই। অনেক মানুষ লাইন ধরতে সংকোচ বোধ করে, ফলে বাস্তব সহায়তা থেকেও বঞ্চিত হন।
অর্থনীতির বর্তমান চিত্র হলো—প্রবৃদ্ধির হার কমেছে, মূল্যস্ফীতি বেশি, আর সামাজিক নিরাপত্তার কাঠামো দুর্বল। এই বাস্তবতায় সঞ্চয়পত্রের সুদহার কমানো সাধারণ মানুষের স্বস্তিকে আরও সংকুচিত করেছে।
সরকার চাইলে সামষ্টিক অর্থনৈতিক ভারসাম্য রক্ষায় সঞ্চয়পত্রের সুদহার হ্রাস করতে পারে, কিন্তু মূল বিবেচনা হওয়া উচিত—মানুষের জীবনযাত্রায় স্বস্তি আনা। তা হতে পারে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ, অথবা পার্সোনাল ফাইন্যান্সের বিকল্প উৎস সৃষ্টি করে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে, বাংলাদেশ এ দুটো ক্ষেত্রেই পিছিয়ে। তাই বর্তমান বাস্তবতায় সুদহার কমানোর সিদ্ধান্ত দেশের সীমিত ও নিম্ন আয়ের মানুষের জন্য আর্থিক চাপ আরও বাড়িয়ে তুলেছে।